
“ঐতিহাসিক দায় থেকে আজকের জবাবদিহি: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং ১৭ নভেম্বরের রায়”
একজন সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়; এটি আমাদের জাতির গভীরতম ক্ষতের নিরাময় এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি একটি ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (International Crimes Tribunal- ICT) গঠনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই বিচার প্রক্রিয়াটি দেশের বিচারিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়।
পটভূমি: ১৯৭১-এর বিচার ও আইনি ভিত্তি
এই বিচার প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩, যা স্বাধীনতার পরপরই প্রণীত হয়েছিল। দীর্ঘ সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই আইনটি কার্যকর হতে প্রায় চার দশক সময় নেয়। অবশেষে, ২০১০ সালে ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে বিচার কাজ শুরু হয়।
এই বিচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুটি:
ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার: ১৯৭১ সালের গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী এবং তাদের সহযোগীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অন্যায়ের বিচার করে দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা।
বিচারের গতিপথ: একাত্তরের অপরাধীদের শাস্তি
ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ১৫ বছরে ১৯৭১ সালের অপরাধের জন্য মোট ৫৭টি মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে। এই রায়গুলোর মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, আব্দুল কাদের মোল্লা এবং বিএনপির নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এই কঠোর শাস্তিগুলো দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক জন-আন্দোলন তৈরি করেছিল এবং বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিল।
আইনি কাঠামো ও তার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ
আইনটির দীর্ঘ পথচলায় বেশ কিছু মৌলিক বিধান যুক্ত ও সংশোধিত হয়েছে:
ক. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর সংশোধনীর বিস্তারিত
আইনটি তার কার্যকারিতার পথচলায় বেশ কয়েকবার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে গেছে। ২০০৯ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সংশোধনের ফলে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি ‘ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর’ বিচারের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধনীটি আসে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ, অভিযোগকারী বা তথ্য প্রদানকারীকেও আপিল করার অধিকার দেওয়া হয় এবং সংস্থা বা সংগঠনের বিচারের বিধান সংযোজিত হয়। সর্বশেষ সংশোধনগুলো ২০২৪ (নভেম্বর) এবং ২০২৫ (ফেব্রুয়ারি) সালে হয়, যা জুলাই অভ্যুত্থানের অপরাধের বিচার দ্রুত করতে প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন আনে।
খ. ট্রায়াল ইন অ্যাবসেনশিয়া (অনুপস্থিতিতে বিচার)
২০১২ সালে সংশোধনের মাধ্যমে এই আইনে ‘ট্রায়াল ইন অ্যাবসেনশিয়া’ (ধারা ১০এ) বিধানটি যুক্ত হয়। এর সারমর্ম হলো: যখন কোনো আসামী জেনেবুঝে পলাতক থাকেন এবং তাকে আইনি প্রক্রিয়ায় হাজির করা সম্ভব হয় না, তখন বিচার প্রক্রিয়া যেন স্থবির না হয়, সেজন্য তার অনুপস্থিতিতেই বিচার চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালকে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে, আদালত আসামীর পক্ষে সরকারের খরচে একজন আইনজীবী (ডিফেন্স কাউন্সেল) নিয়োগ করেন।
গ. সুপিরিয়র কমান্ড রেসপনসিবিলিটি (ঊর্ধ্বতন কমান্ডের দায়বদ্ধতা)
এই আইনটির প্রবর্তন লগ্ন থেকেই ধারা ৩(২)-এর উপধারা (এ)-তে এই নীতিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মূল কথা হলো: কোনো সামরিক বা বেসামরিক ঊর্ধ্বতন নেতা তার অধীনস্থদের অপরাধের জন্য দায়ী হবেন, যদি তিনি অপরাধটি জানতেন (বা জানার মতো পরিস্থিতি ছিল) এবং তা প্রতিরোধ করতে বা অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন। এই নীতির কারণে উচ্চ পদে থাকা পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
বিতর্ক ও সমালোচনা: একটি অনিবার্য প্রশ্ন
এই বিচার প্রক্রিয়াটি দেশে-বিদেশে নানা সমালোচনার মুখে পড়েছে। অভিযোগ ছিল যে এটি দেশীয় আইন হওয়ায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে পুরোপুরি সমমানের নয়। এছাড়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার, ২০১২ সালের স্কাইপ বিতর্ক, এবং দণ্ডপ্রাপ্তদের আইনজীবী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার ঘাটতির অভিযোগও উঠেছিল। তবে, বিচার সংশ্লিষ্টরা সবসময়ই দাবি করেছেন যে, আপিল ও রিভিউ প্রক্রিয়া পর্যন্ত সুযোগ থাকায় বিচারটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ ছিল।
আজকের রায়: এক নতুন বিচারিক অধ্যায় (১৭ নভেম্বর, ২০২৫)
১৭ নভেম্বর, ২০২৫-এর রায়টি বাংলাদেশের বিচারিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। এটি ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার।
দণ্ডপ্রাপ্ত: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজন আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
দণ্ডের প্রকৃতি: ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে ‘সুপিরিয়র কমান্ড রেসপনসিবিলিটি’ নীতির ভিত্তিতে এক নম্বর অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া, অন্য তিনটি গুরুতর অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অভূতপূর্ব নির্দেশনা: রায়ে একইসঙ্গে দণ্ডপ্রাপ্তদের সম্পদ জব্দ এবং জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই রায়টি একটি শক্তিশালী বার্তা দেয় যে, মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক পদমর্যাদাই দায়মুক্তির কারণ হতে পারে না।
অব্যাহত ন্যায়বিচারের পথ
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিক দায় থেকে শুরু হয়ে এখন আধুনিক জনদাবির প্রতিও প্রসারিত হয়েছে। প্রতিটি রায়, আইনি সংশোধন এবং আইনি পদক্ষেপ জাতিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিচ্ছে। ১৭ নভেম্বরের রায় প্রমাণ করে যে, ট্রাইব্যুনাল অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমানের অপরাধের ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত। তবে, এই রায়ের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করবে উচ্চ আদালতের আপিল, রিভিউ এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মতো আইনি ধাপগুলোর ওপর। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই শিক্ষাই রেখে যাবে যে, আইনের শাসন সর্বদা অটুট থাকবে এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।
লেখক,
জিয়াউর রহমান মুকুল,
এডভোকেট,
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট,
ইমেল:[email protected]
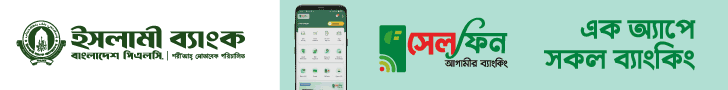










পাঠকের মতামত